ট্র্যাডিশনাল সিস্টেমে শুধুমাত্র “লক্ষণ” (symptom) দেখা হয়, শিশুর সামগ্রিক অবস্থা নয়।
শরীর, মন, ও গাট হেলথ — এই তিন দিক একত্রে দেখা হয় না।
প্রাকৃতিক বা খাদ্যভিত্তিক পদ্ধতি প্রায় অনুপস্থিত।
সবকিছুই ওষুধ-কেন্দ্রিক — হিলিং নয়, “control” করাই লক্ষ্য।
ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয় না।
ওষুধ বন্ধ করলে অনেক সময় শিশুর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।
নিউরোপ্লাস্টিসিটি বা ব্রেইন রিওয়ারিং নিয়ে কোনো ধারণা নেই।
শিশুর এনজাইটি বা সেন্সরি ওভারলোড ওষুধে ঢেকে রাখা হয়।
শিশুর গাট সমস্যা বা ফুড সেনসিটিভিটি বিবেচনায় নেওয়া হয় না।
শিশুর প্রাকৃতিক স্বভাবের পরিবর্তে “normal” বানানোর চেষ্টা করা হয়।

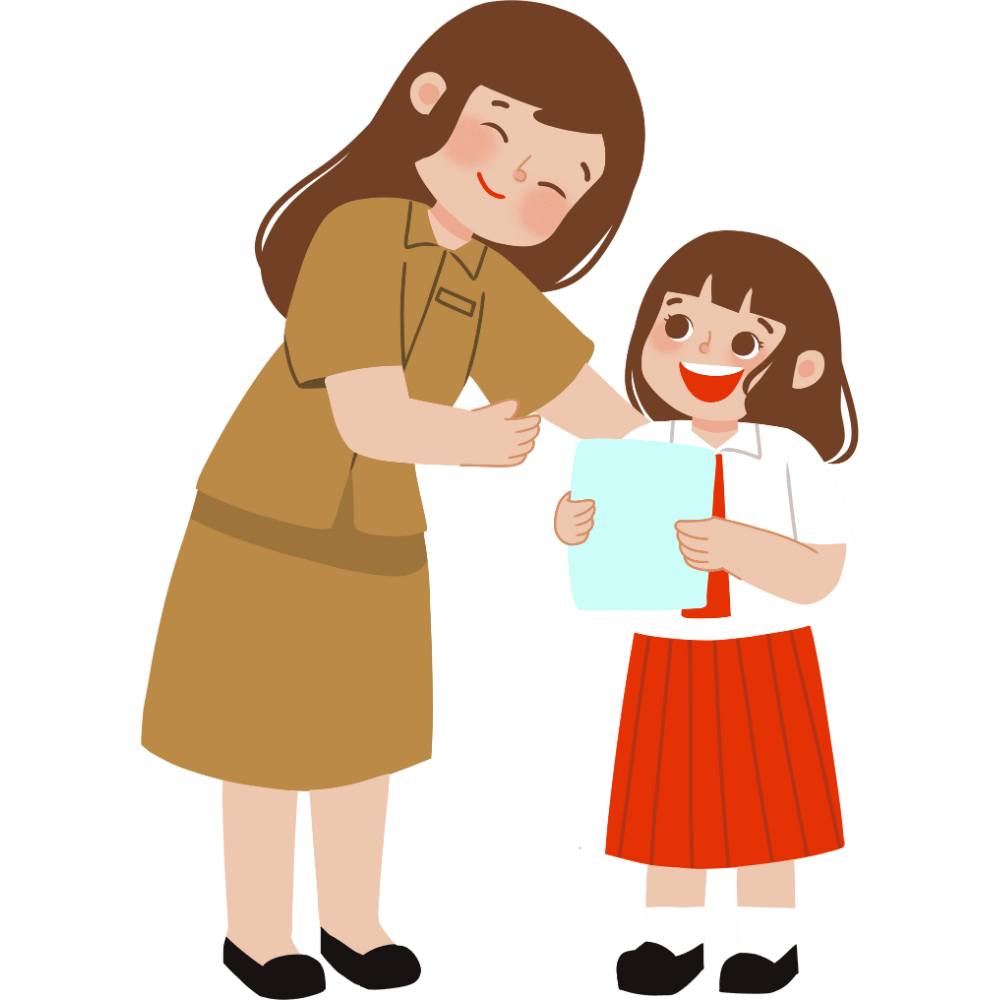
প্যারেন্টকে বাইরে রেখে থেরাপি করা হয় — শিশুর উন্নতি টেকসই হয় না।
বাবা-মাকে শেখানো হয় না “বাড়িতে কীভাবে সাহায্য করতে হবে।”
থেরাপির সময় বাবা-মা জানে না শিশুকে ঠিক কী শেখানো হচ্ছে।
প্যারেন্টকে সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয় না।
অনেক থেরাপিস্ট প্যারেন্টের প্রশ্ন শুনতে বা ব্যাখ্যা দিতে চায় না।
শিশুর রিপোর্ট বা প্রগ্রেসে স্বচ্ছতা থাকে না।
থেরাপিস্ট-নির্ভর পদ্ধতি প্যারেন্টকে অসহায় করে তোলে।
শিশুর আচরণ পরিবর্তন হলেও বাবা-মা জানে না কিভাবে বজায় রাখতে হবে।
বাড়িতে প্রয়োগ করার মতো কোনো গাইডলাইন দেওয়া হয় না।
প্যারেন্টকে “problem creator” ভেবে দোষারোপ করা হয়।
অধিকাংশ ভালো সেন্টার শুধু ঢাকায় বা বড় শহরে অবস্থিত।
গ্রামীণ পরিবারকে দূর-দূরান্তে যাত্রা করতে হয়।
দীর্ঘ ভ্রমণে শিশুর overstimulation ঘটে।
প্রতিবার থেরাপির জন্য অনেক সময় নষ্ট হয়।
সেন্টার পৌঁছাতে ট্রাফিক ও ভিড় শিশুর anxiety বাড়ায়।
প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবার সঠিক থেরাপি পায় না।
অনুপস্থিতিতে সেশন বাদ পড়লে continuity নষ্ট হয়।
অনলাইন অপশন না থাকায় ফলো-আপ হয় না।
ভ্রমণ ও লজিং খরচ পরিবারের উপর বাড়তি চাপ ফেলে।
শিশুর নিজের পরিচিত পরিবেশের বাইরে কাজ করায় সে অস্বস্তি বোধ করে।
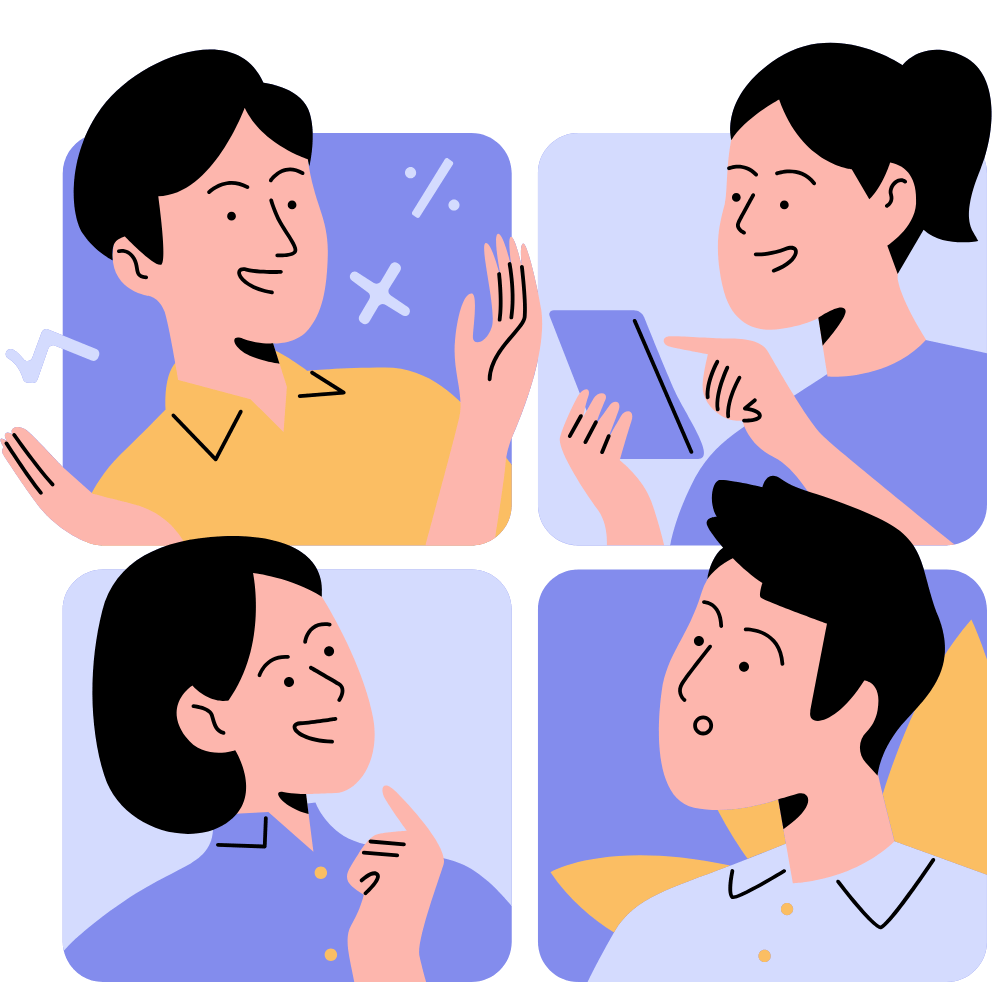

থেরাপি ফি অত্যধিক, অথচ ফল অনিশ্চিত।
প্রতিটি সেন্টারের খরচ ভিন্ন, মান এক নয়।
অপ্রয়োজনীয় টেস্ট বা সেশন যুক্ত করে বাড়তি খরচ নেয়।
সরকারি কোনো ভর্তুকি বা ইনস্যুরেন্স সাপোর্ট নেই।
যাতায়াত, অপেক্ষা ও ছুটি নেওয়ায় চাকরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
প্যারেন্টরা অনেক সময় কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।
ছোট শিশুদের জন্য নির্ভরযোগ্য ডে-কেয়ার নেই।
প্রাইভেট সেন্টারের রুল অনুযায়ী পেমেন্ট করতে হয় — ফেরতযোগ্য নয়।
মাঝপথে থেরাপিস্ট পরিবর্তন হলে আবার নতুন খরচ।
সময় ও অর্থ দুই দিকেই ক্লান্তি আসে।
বাবা-মাকে কখনোই কাউন্সেলিং দেওয়া হয় না।
“আপনার বাচ্চা স্বাভাবিক না” — এমন মনোবল-ভাঙা মন্তব্য সাধারণ।
হতাশা, অপরাধবোধ ও আত্মদোষবোধ বেড়ে যায়।
পরিবার ও সমাজে লজ্জা বা কলঙ্কের চাপ থাকে।
বাবা-মা একাকিত্ব অনুভব করেন — কোনো পিয়ার সাপোর্ট নেই।
একাধিক ডাক্তার বা থেরাপিস্টের বিপরীত মতামতে বিভ্রান্তি।
শিশুর উন্নতি না হলে প্যারেন্টদের দায়ী করা হয়।
শিশুর অগ্রগতির জন্য অপেক্ষা করতে করতে মানসিক ক্লান্তি আসে।
প্যারেন্টদের মধ্যে দাম্পত্য চাপ ও সম্পর্ক ভাঙনের ঝুঁকি।
শিশুর প্রতি ভালোবাসার জায়গায় হতাশা জমে।
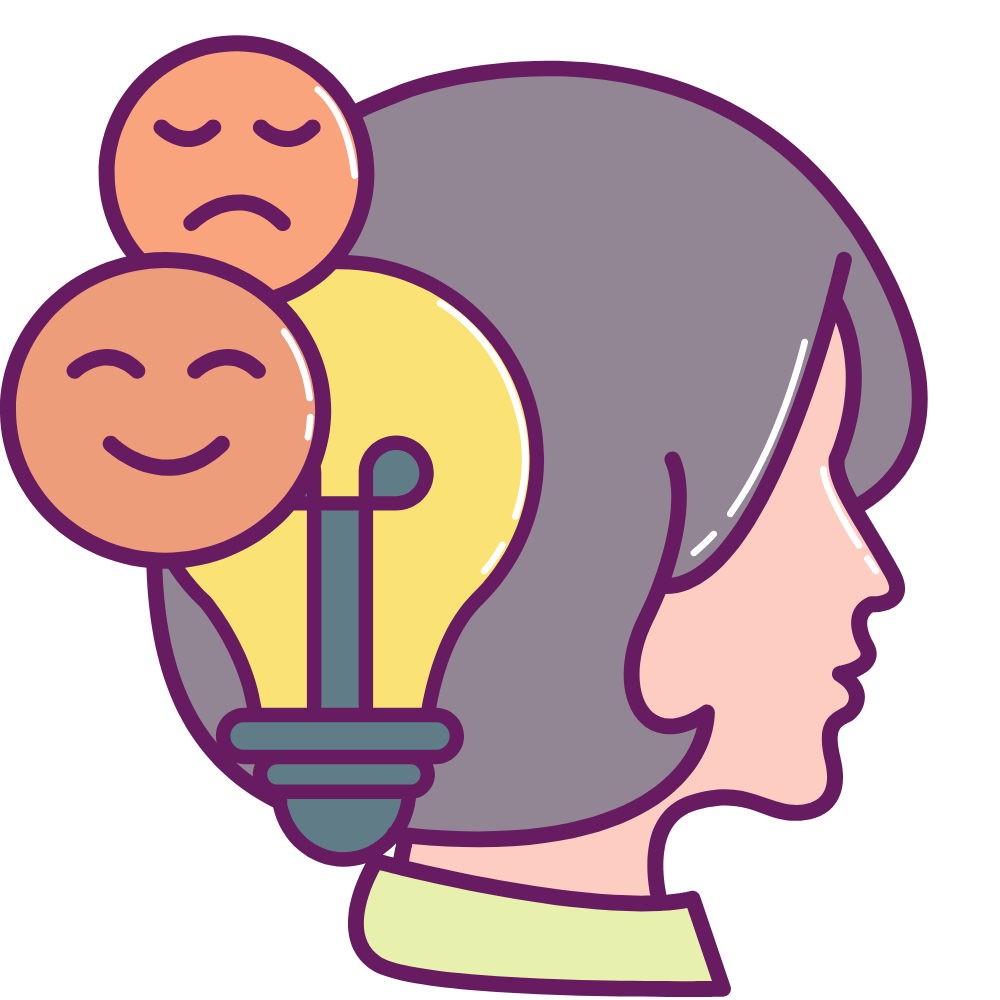
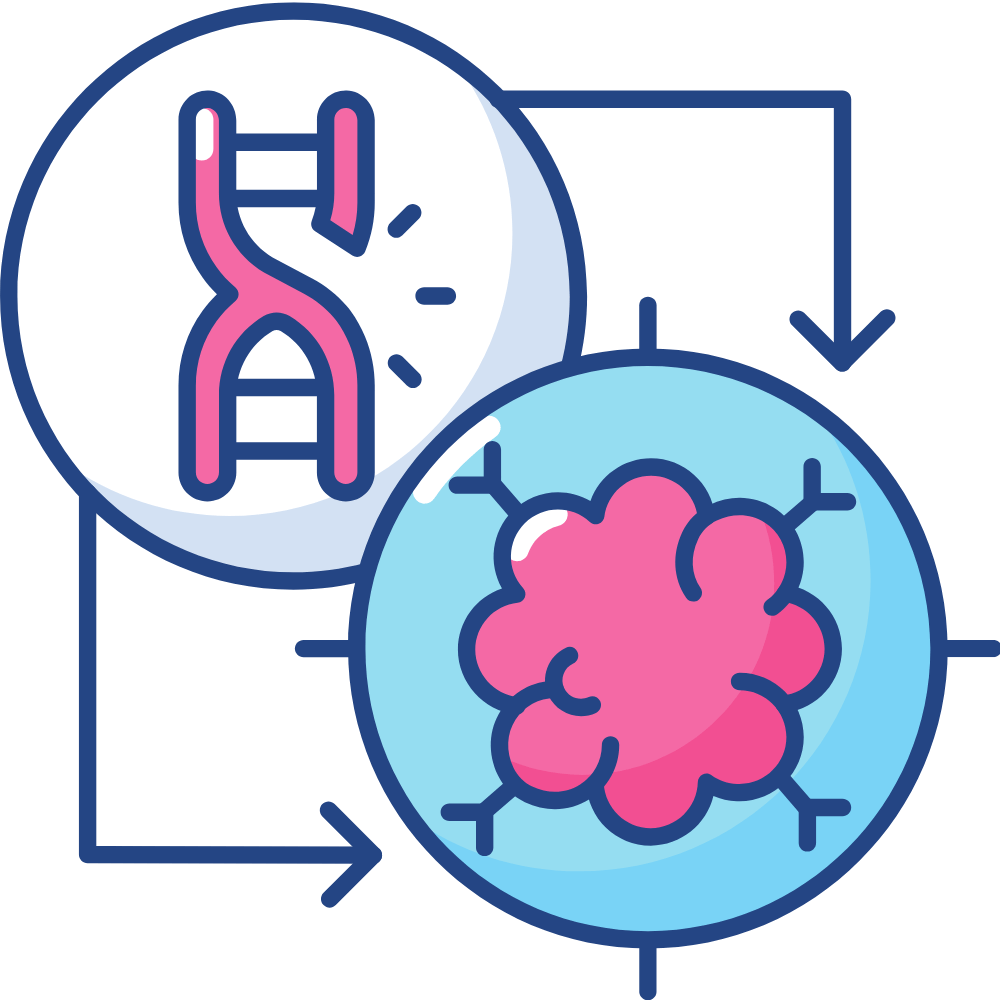
গাট-ব্রেইন কানেকশন নিয়ে সচেতনতা প্রায় নেই।
খাদ্য বা পরিবেশের প্রভাব নিয়ে গবেষণা হয় না।
গ্লুটেন/কেজিন ইস্যুকে “মিথ” বলা হয়, পরীক্ষা করা হয় না।
নিউরোপ্লাস্টিসিটি-ভিত্তিক থেরাপি এখনো চালু হয়নি।
শিশুদের ডায়েট একেবারেই অবহেলিত।
হাইপারঅ্যাক্টিভিটি হলে ওষুধ—কারণ নয়, ফল দেখা হয়।
খাদ্য সংবেদনশীলতা বা ইনফ্ল্যামেশন পরিমাপের সুযোগ নেই।
“ডিটক্স” ধারণা নিয়ে কোনো মেডিক্যাল গাইডেন্স নেই।
ওষুধের সাইড-ইফেক্ট ম্যানেজ করতে হয় নিজের মতো করে।
চিকিৎসা ব্যবস্থা একমুখী ও পুরনো চিন্তাধারায় আটকে আছে।
থেরাপিস্টদের অনেকেই আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং পাননি।
প্যারেন্ট-এডুকেশন প্রোগ্রাম অনুপস্থিত।
পরিবারকে ব্রেইন-বেসড শিক্ষা দেওয়া হয় না।
বাংলা ভাষায় রিসোর্স বা গাইডলাইন পাওয়া যায় না।
শিশুর জন্য থেরাপি একঘেয়ে — একই টাস্ক বারবার।
শিক্ষামূলক ব্যাখ্যা ছাড়া শুধু “অ্যাক্টিভিটি” করানো হয়।
প্যারেন্টদের জন্য ভিডিও বা রেকর্ডেড মেটিরিয়াল নেই।
স্কুলের শিক্ষকরা জানেন না কিভাবে এমন শিশু সামলাতে হয়।
হোমওয়ার্ক বা হোম-ফলোআপের কোনো সিস্টেম নেই।
দীর্ঘমেয়াদে উন্নতি মাপার কোনো মানদণ্ড নেই।
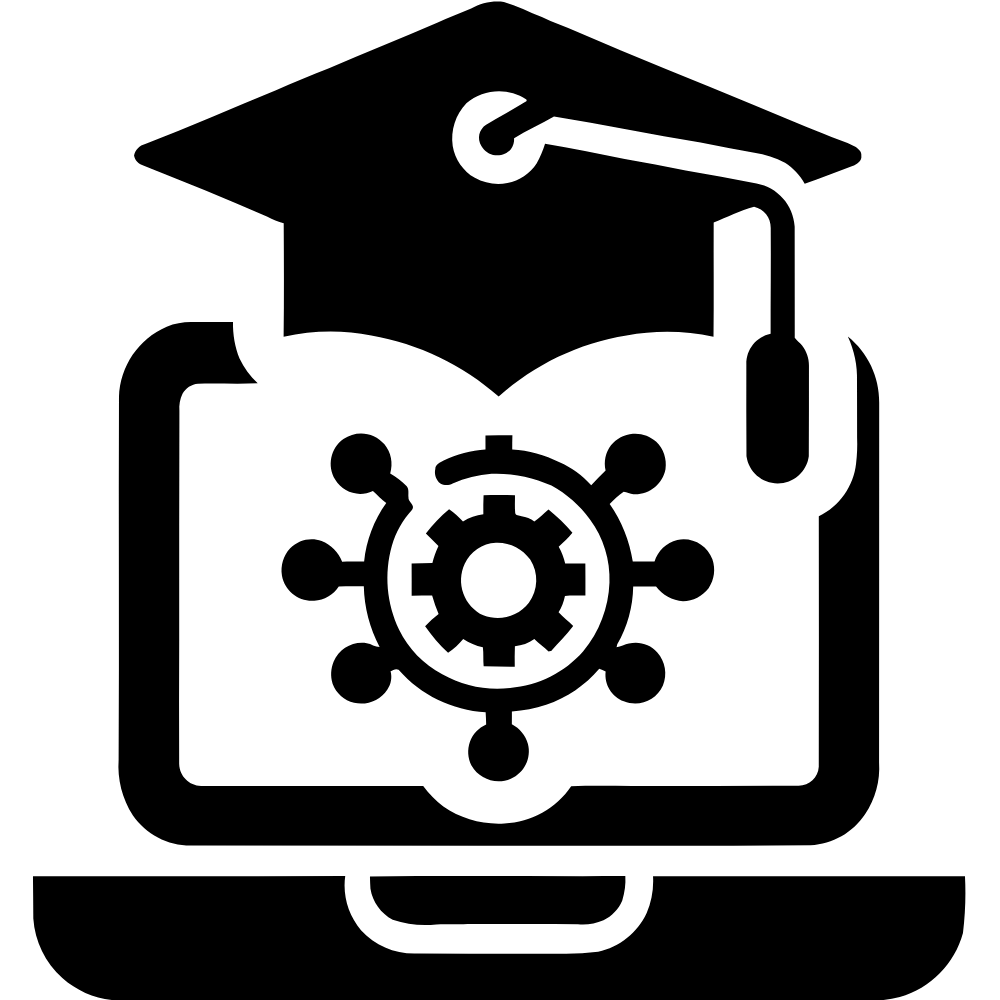

কোনো শক্তিশালী প্যারেন্ট কমিউনিটি নেই।
অভিজ্ঞ বাবা-মা নতুনদের সাহায্য করেন না — সিস্টেমে সংযোগ নেই।
সমস্যার কথা বললে “অতিরঞ্জন” বলা হয়।
গ্রুপ-সাপোর্ট বা কাউন্সেলিং সেশন বিরল।
প্যারেন্টদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে কেউ নজর দেয় না।
পরিবারে আত্মীয়রা সহযোগিতা না করে সমালোচনা করে।
শিশুর স্কুলে সহপাঠীরা তাকে আলাদা করে রাখে।
সেন্টারগুলো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব রাখে — সহযোগী নয়।
প্যারেন্টরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না।
শিশু-ফ্রেন্ডলি পরিবেশ কম, judgemental আচরণ বেশি।
বিদেশি মডেল কপি করা হয়, বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না।
ডায়েট চার্টে এমন খাবার থাকে যা এখানে পাওয়া যায় না।
ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ উপেক্ষা করা হয়।
প্যারেন্টদের সময়, অর্থ ও জীবনযাত্রা বিবেচনা করা হয় না।
পরিবারে একাধিক সদস্য থাকায় রুটিন বাস্তবায়ন কঠিন হয়।
লোকাল ভাষায় সচেতনতা প্রোগ্রাম নেই।
সরকারি হাসপাতালে কোনো ডেডিকেটেড Autism ইউনিট নেই।
সরকারি মেডিকেল স্টাফদের এই বিষয়ে পর্যাপ্ত ট্রেনিং নেই।
রোগ নির্ণয়ের জন্য বিদেশে যেতে হয় অনেক পরিবারকে।
দেশীয় সমাধানের অভাবে পরিবার বিদেশি থেরাপিতে নির্ভরশীল হয়।
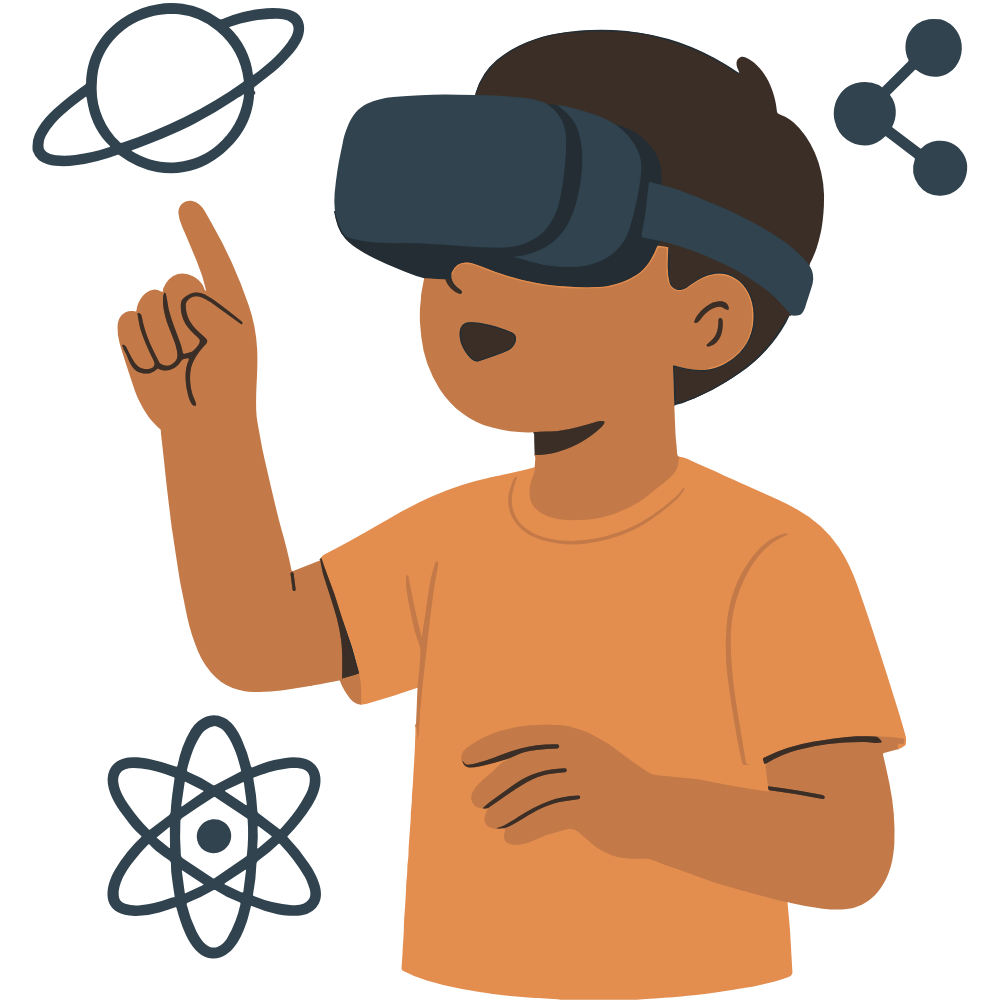

বছরের পর বছর থেরাপি চলেও শিশুর উন্নতি সামান্য।
থেরাপি বন্ধ করলে দ্রুত regression দেখা দেয়।
শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ে না — কৃত্রিম শেখানো হয়।
আচরণিক উন্নতি হলেও মানসিক বিকাশ হয় না।
পরিবারে শান্তি আসে না — চাপ থেকেই যায়।
শিশুর self-regulation শেখানো হয় না।
পরিবারে আধ্যাত্মিক বা মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসে না।
বাবা-মা “থেমে নেই” এমন অনুভব করেন।
শিশুর ভবিষ্যত নিয়ে ভয় থেকেই যায়।
“হিলিং” নয়, শুধু “ম্যানেজমেন্ট” হয় — স্থায়ী সমাধান নয়।

Disclaimer: GAT-PSM is a holistic parenting and lifestyle development program — not a medical or therapeutic service.
© 2025 greatleafbd.com all rights reserved